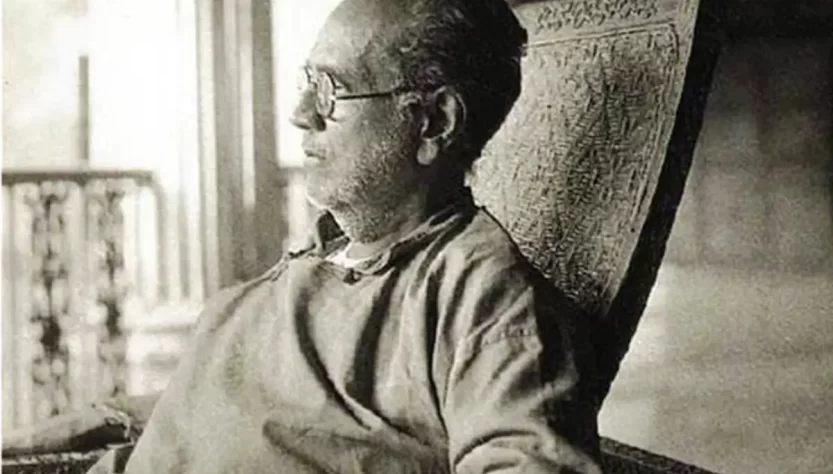‘শনিবারের চিঠি’ থেকে একটি ফোন এল— একটা লেখা চাই। কিংবদন্তি চিত্রশিল্পী, শিল্পগুরু, লেখক, কাটুম কুটুম ও বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলির স্রষ্টা; ভারতীয় শিল্পের পথিকৃৎ শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ওপর। আমার এই মুহূর্তে যা মনে হচ্ছে, তা বলেই ফেলি! এই পুষ্করিণীর জল আঁজলা ভরে সেঁচে ফেলা অথবা যদি বলি বালুয়াড়িতে কতগুলি বালি আছে আমাদের জানাও— তা যেমন অসম্ভব তেমনি না বুঝে কাজে ঝাঁপ দেওয়ার অর্থ মূর্খামি। তবু এতদিন শিল্পচর্চা করেছি, শিল্প অধ্যাপনা করেছি, তাই কিছু লিখতে তো হবেই।
যদি বলি— পুজো আয়োজন অনেক— প্যান্ডেল বাঁধ রে, চাঁদা তোলো, প্রতিমা আনা— পুজোর মণ্ডপে বসাও প্রতিমা, মণ্ডপ সাজানো, আরও কতরকমের কাজ। আলোয় আলোয় ভরে উঠল মণ্ডপ, পুরুতঠাকুর এলেন, পুজো উপাচার এল। ফুল, বেলপাতা, গঙ্গাজল দিয়ে মন্ত্র পড়ে পুজো হল, আবেগে ভক্তিতে ভাসলাম— কিন্তু প্রসাদ কণিকামাত্র। তার পরই বিসর্জন। কিন্তু মনে যে ছবিটি আঁকা হল—তা তো হল চিরস্থায়ী। আর যতদিন মনের কোটরে জমা থাকবে তত হবে মধুর। এই সঞ্চিত মধু শিল্পের রূপ নিয়ে চিত্রে বা ভাস্কর্যে ধরা দেবে শিল্পীর কাছে।
…চমকে মুখ তুলে চেয়ে দেখি সামনে আকাশ লাল টকটক করছে, সূর্যোদয় হচ্ছে। সে কী রঙের বাহার, মনে হল যেন সৃষ্টিকর্তার গায়ে জ্যোতি ছড়িয়ে দিয়ে সূর্যদেব উদয় হচ্ছেন। সৃষ্টিরক্ষার এ প্রভা চোখ মেলে না দেখে আমি কিনা চোখ বুজে তাঁকে দেখতে চেষ্টা করছিলুম। সেদিন বুঝলুম আমার রাস্তা এ নয়; চোখ বুজে তাঁকে দেখতে যাওয়া আমার ভুল। শিল্পী আমি, দু’চোখ মেলে তাঁকে দেখে যাব জীবনভোর।…
অবনীন্দ্রনাথের শিল্পচর্চাও ঠিক এইভাবেই ধরা দিয়েছিল। ছেলেবেলায় লেখাপড়ায় তেমন মন নেই। শিশুমন দৌড়ে বেড়ায় লতা-পাতা গাছ-গাছালিতে। কাঠবিড়ালের ডোরাকাটা লেজ তুলে ডালে ডালে দৌড়— সে ভারী মজার। মন মেতে ওঠে এই মজায়। তবুও লেখাপড়া করেছেন সংস্কৃত কলেজে এবং অন্যান্য স্কুলেও। রানী চন্দ্রকে বলেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ, ‘ধ্যান-ধারণা, পুজো আর্চা, সে কোনদিন করিনে।’ কিন্তু একবার হল কঠিন রোগ। ‘লিভার থেকে বুক অবধি যেন অগ্নি শূল বিঁধছে’। অসহ্য যন্ত্রণায় শিল্পী কাতর। ডাক্তারেরা অসহায়, ব্যর্থকাম। এমন সময় রাত্রে স্বপ্ন দেখলেন— মা এসেছেন, ব্যথার জায়গায় হাত বুলোলেন; — আর সব সেরে গেল জেগে উঠতেই। কী আশ্চর্য অনুভূতি। তাই জেগে উঠেই মনে করলেন সকালবেলায় নিরিবিলিতে ভগবানের নাম জপ করা দরকার। ভাবনা আর কাজ হাতে-নাতে শুরু। “ভগবানের একটা রূপ কল্পনা করে নিয়ে বলতে লাগলুম— এতদিন তোমায় ডাকিনি, বড় ভুল হয়েছে। দয়াময় প্রভু ক্ষমা করো আমায়। এমনি সব ছেলেমানুষি কথা। আর চেষ্টা চলছে প্রাণে ভাব জাগিয়ে চোখে দু’ফোঁটা জল যদি আনতে পারি। এমন সময় মনে হল কানের কাছে কে যেন বলে উঠল, ‘চোখ বুজে কি দেখছিস, চোখ মেলে দেখ।’ চমকে মুখ তুলে চেয়ে দেখি সামনে আকাশ লাল টকটক করছে, সূর্যোদয় হচ্ছে। সে কী রঙের বাহার, মনে হল যেন সৃষ্টিকর্তার গায়ে জ্যোতি ছড়িয়ে দিয়ে সূর্যদেব উদয় হচ্ছেন। সৃষ্টিরক্ষার এ প্রভা চোখ মেলে না দেখে আমি কিনা চোখ বুজে তাঁকে দেখতে চেষ্টা করছিলুম। সেদিন বুঝলুম আমার রাস্তা এ নয়; চোখ বুজে তাঁকে দেখতে যাওয়া আমার ভুল। শিল্পী আমি, দু’চোখ মেলে তাঁকে দেখে যাব জীবনভোর।”
এই উপলব্ধি বোধ থেকে এই কথায় আসা যায়, শিল্পী শুধু নয়ন ভরে দেখে যাবে, আর হৃদয়ে সঞ্চয় করবে সেই পরম ধন। যা যে কোনও মুহূর্তে খুলে দেবে তার হৃদয়ের দ্বার, সে নানাভাবে ভাঙবে, গড়বে, ঘষামাজা করে নতুন কিছু করার তাগিদে ভেঙে খান খান হবে, তবেই না হবে নতুন সৃষ্টি। হয়তো বা না কিছুই। চেপেচুপে ধরবে জেদ—আত্মশ্লাঘা। নিস্তার নেই। দিনে রাত্রে চলবে নিপীড়ন, কখন ধরা দেবে সে এই আশাই জাগিয়ে রাখবে মনকে। তবেই তো খোঁজ পাবে সেই পরমরতন।
যা অবনীন্দ্রনাথ দেখতে পেয়েছিলেন সৃষ্টিকর্তার গায়ের জ্যোতি। সৃষ্টিকর্তার এই প্রভাবমণ্ডল যে সত্যিকারের দেখেছে, তার হৃদয়ে আর কোনও মলিনতা নেই। আপনা থেকে পদ্মের পাপড়ি খুলতে খুলতে শতদলের রূপ নেবে, হবে শিল্পীর জীবন ধন্য— শিল্প করার সার্থকতা, তখনই শিল্পী তার চারদিক ছড়িয়ে, দর্শকদের মোহিত করে শিল্পের পূর্ণতা লাভ করবে। সেই হবে প্রকৃত শিল্পী— তার চলনে বলনে ছলকে ছলকে পড়বে শিল্প অমৃতধারা। যাঁরা নয়ন ভরে পান করে হৃদয়ে ধরে রাখবেন তাঁরা শুধু একটি কথাই বারে বারে বলবেন— ‘যা দেখিলাম, তা জন্ম-জন্মান্তরেও ভুলিব না।’ এখানেই শিল্পের ও শিল্পীর সার্থকতা। এখানেই অবনীন্দ্রনাথ সার্থক শিল্পী। তিনি শিল্পগুরু।
তখন তিনি এক ভারতীয় নতুন পথের অনুসন্ধান করছেন। আর বুনে চলছেন নতুন নতুন স্বপ্নের জাল, আর তখনই আবিষ্কার করলেন দেশীয় শিল্পের রহস্যের মায়াজাল। এই মায়াজালে অবনীন্দ্রনাথ গড়ে তুলতে চাইলেন ভারত শিল্পের আত্মকথা। ঠিক এই সময়ই রবীন্দ্রনাথ আর একটু সংযোজন করলেন বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের কবিতাকে চিত্রেশিল্পে রূপ দিতে। অবনীন্দ্র-ভাবনায় দুয়ে মিলে এক হয়ে গেল।
এবার একটু অন্যকথায় আসি। সৃষ্টিকর্তার গায়ে জ্যোতি এবং প্রভা দেখেই কি তিনি শিল্পগুরু হয়ে উঠলেন? তা তো হয় না। তাহলে শিল্পী হয়ে ওঠার অনুকূলে বা প্রতিকূলে আর কী কী ছিল। যেমন লেখাপড়া করতে হলে একটি প্রতিষ্ঠানের বা শিক্ষাঙ্গনের দরকার হয়, তিনি কি সেই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করেননি? কলকাতায় তখন তিন দশক আগে সরকারি আর্ট স্কুল শুরু হয়েছে। বিদেশ থেকে শিল্পশিক্ষক আসছেন সরকারি আর্ট স্কুলে। এই সময় নয়ের দশকে শিল্পী গিলার্ডির কাছে কাজ শিখেছেন। ড্রইং-এর হাত তখন বেশ দৃঢ়। পাশ্চাত্য শিল্পে অনুশীলন ও চর্চার সঙ্গে এদেশের অন্তর আত্মার নির্যাস ধরার নানা ভাবনা চালিয়ে গেছেন। এই পথ খোঁজাই ঠাকুরবাড়ির রক্ত-মজ্জায়, অস্তিত্বে। তাঁকে সাহস জুগিয়েছে কথকতা, কীর্তন, পালাপার্বণ। তাই এক ভারতীয় নতুন পথের অনুসন্ধান করছেন। আর বুনে চলছেন নতুন নতুন স্বপ্নের জাল, আর তখনই আবিষ্কার করলেন দেশীয় শিল্পের রহস্যের মায়াজাল। এই মায়াজালে অবনীন্দ্রনাথ গড়ে তুলতে চাইলেন ভারত শিল্পের আত্মকথা। ঠিক এই সময়ই রবীন্দ্রনাথ আর একটু সংযোজন করলেন বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের কবিতাকে চিত্রেশিল্পে রূপ দিতে। অবনীন্দ্র-ভাবনায় দুয়ে মিলে এক হয়ে গেল। সৃষ্টির সঙ্গে স্রষ্টার—আর স্রষ্টার সঙ্গে সৃষ্টির। এ দুয়ে দুয়ে চার নয়—একেবারে ষোলোকলায় পূর্ণ হল, স্বপ্নের নতুন নাও বাওয়া। ধীরে ধীরে অবনীন্দ্রনাথ ফুটে উঠলেন ভারতীয় নতুন ধারার প্রবর্তক হয়ে। গড়ে উঠল চিত্রের মাধ্যমে ঈশ্বর উপাসনা।
মোগল চিত্রকলা, রাজপুত চিত্রকলা, কুলু, কাংড়া এবং পুঁথি চিত্রমালায় তো ভারতীয় ভাব, ধ্যান-ধারণা আছেই, কিন্তু সমসাময়িক ভাবনার এক নতুন রূপ খুঁজছেন অবনীন্দ্রনাথ। এই সময় কলকাতার আর্ট স্কুলে অধ্যক্ষ হয়ে এলেন ই.বি. হ্যাভেল। তিনি ভারতের সব মন্দির, ভাস্কর্য, অজন্তার চিত্রমালা দেখে স্তম্ভিত। এত সমৃদ্ধ চিত্রকলা যে দেশে তৈরি হয়, মানুষজন, জীবনযাত্রা, ভাবনার বৈচিত্র, সেখানে শুধু পাশ্চাত্য ভাবনায় ভাবিত হবে কেন এখানকার শিল্পীরা? তাই আর্ট স্কুলে একটি ভারতীয় শিল্পবিভাগ গড়ে তুললেন। হ্যাভেলের নজর ছিল ঠাকুরবাড়ির শিল্পীদের উপর। তিনি অবনীন্দ্রনাথের শরণাপন্ন হলেন। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ একটু সবার আড়ালে নিজের মতো থাকতে ভালবাসেন। নিজের মতো ছবি আঁকেন। তাতেই তিনি খুশি। তিনি জানতে পারলেন অবনীন্দ্রনাথ তাঁর মায়ের কথা ফেলতে পারবেন না। তাই হ্যাভেল, অবনীন্দ্রনাথের মায়ের শরণাপন্ন হলেন। মাকে রাজি করিয়ে, অবনীন্দ্রনাথকে আর্ট স্কুলের ভারতীয় বিভাগের (ইন্ডিয়ান পেন্টিং) প্রধান করলেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে অবনীন্দ্র-সান্নিধ্যলাভে ভারতীয় বিভাগে পঞ্চপাণ্ডবের আবির্ভাব। তাঁরা এক-একজন শিল্পজগতের দিকপাল। সারা ভারতভূমে ছড়িয়ে পড়ল অবনীন্দ্র-দ্যুতি। নন্দলাল বসলু, অসিতকুমার হালদার, ক্ষিতিমোহন মজুমদার, ঈশ্বরীপ্রসাদ গুপ্ত, শৈলেন্দ্রনাথ দে। এই পঞ্চপাণ্ডব ছাড়া আরও অনেকে ভারতীয় চিত্রকলার ধারাকে সমৃদ্ধ করেছেন।
বিংশ শতাব্দীর গোড়াতেই স্বদেশী আন্দোলন। শিল্পীমনে অনেক কিছু স্পর্শ করলেও শিল্পী মনের আকুতিতে গড়ে তুললেন ‘ভারতমাতা’। অনবদ্য এক শিল্পরূপ। শিল্প গড়ে ওঠে কারণে। এই যে দেশাত্মবোধ তখন ভারতবাসীর মর্মে মর্মে প্রবেশ করেছে। বিভিন্ন কারণে হ্যাভেল সাহেবকে অধ্যক্ষের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হল। বাঁধনে বেঁধে থাকা ওঁর স্বভাব নয়, তাই অবনীন্দ্রনাথ আর্ট স্কুলের চাকরি ছাড়লেন। ওরিয়েন্টাল আর্ট স্কুলও ছাত্রদের হাতে তুলে দিলেন। ভাবুক লোক, মেজাজি মানুষও। কিন্তু বড় শিশুমন। সবসময় বালকের মতো খুঁজে বেড়ান বিশ্বচরাচরে শিল্পের মণিরত্ন। তাতেই মশগুল। কোথাও একটা গাছের ডাল। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে রূপের সন্ধান করেন। এ এক নতুন খেলা। তবে মনের আনন্দে মেতেই আছেন। রং ও রেখায় ওয়াশের ছবিগুলি এক মায়াময় অতলস্পর্শী। কোথায় সেই দুরন্ত ছেলে, যার দস্যিপনা বুঝে ওঠা ভার কিন্তু ছবিতে সে শান্ত, ধ্যানমগ্ন, নিরুত্তাপ। যেন রং-এর পরতে পরতে মনের বিস্তার। তেমনি নিজের লেখা সম্পর্কে শিল্পী নিজে বলেছেন—‘আমি গান বাঁধি, ছড়ার গান, যাত্রার গান— আর রবিকা গান বাঁধেন, পড়ার গান।’এখানেই অবনীন্দ্রনাথ শিল্পী। একটি গান লেখা, দেখার ও শোনার আর একটি পড়ে উপভোগ করার। অবনীন্দ্রনাথের এই উপলব্ধি শিল্প উপলব্ধির কথা ভাবায়। তাই বলতে কোনও দ্বিধা নেই লেখায় তিনি চিত্রিত করেছেন রং ও তুলি দিয়ে যে বর্ণলেপনে, তাঁর যে আকুতি, তার যে বর্ণময় বিস্তারের অনুভূতি। সেই ধ্যানের কথাই আবার মনে করিয়ে দেয়।
অবনীন্দ্রনাথ আর চাকরিতে বাঁধা পড়তে নারাজ। কিন্তু আশুতোষ ছাড়বেন না। আশুতোষ বলেছিলেন— অবনবাবু, আপনি বছরে দুটো বক্তৃতা দেবেন, আমরা সকলে শুনে ধন্য হব। মাইনে নিয়ে কাজের কথা উঠতেই আশুতোষ বলেছিলেন— মাইনে নয়, ও তো অর্ঘ্য। অবনীন্দ্রনাথ স্যর আশুতোষের ব্যক্তিত্বের মাধুর্যে মুগ্ধ হযেছিলেন। স্যার আশুতোষের অনুরোধে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বাগেশ্বরী অধ্যাপক।
অনেক কথাই লেখা যায় না। ‘মোর ভাবনা কি হাওয়ায় মাতালো’। অবনীন্দ্রনাথ ছিলেন একজন আত্মভোলা লোক। শুধু স্কুল-কলেজ পাশ করলে সব কিছু হয় না। শুধু গলাধঃকরণ করে উদগার করলেও হয় না, চাই আত্মস্থ করা, মন্থনে ক্ষীর তোলা, সেই ক্ষীরকে কীভাবে পরিবেশন করা হবে বা করব সেটাই বড় কথা। সেখানেই বিদ্যার প্রয়োগ। এই অধীত বিদ্যার প্রয়োগের যে রহস্যভেদ এটাই অবনীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য।
অলকেন্দ্রনাথ বলেছেন— ‘বই পড়ে তার মধ্যে একেবারে ডুবে যেতেন।’ এই ডুবে যাওয়ার একটা উদাহরণ দিয়েছেন তিনি। রবীন্দ্রনাথ একবার য়ুরোপ ভ্রমণ করে ফিরে ‘অবন’কে অনুযোগের সুরেই বললেন, সারা য়ুরোপ জুড়ে ওঁর কত ভক্ত। নিজের শিল্প রচনার সিদ্ধির জন্যও তাঁর ওইসব দেশ ঘুরে আসা উচিত; বিশেষ করে প্যারিসের ‘ল্যাটিন কোয়ার্টার’ প্রভৃতি দেখে আসা নিতান্তই প্রয়োজন। তখন নাকি অবনীন্দ্রনাথ তাঁর গড়গড়ার নলে খুব খানিকটা ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, ‘আমি শিল্পী, মানস-চক্ষে সব দেখতে পাই ঐ ধোঁয়ার মধ্যে। হুগো আর বালজাক যখন পড়েই নিয়েছি, তখন আর নিজের চোখে প্যারিস দেখার দরকার হবেনা। তুমি আমাকে বল, আমি হুবহু ল্যাটিন, কোয়ার্টারের ছবি এঁকে দিচ্ছি।’ নিজের অধীত বিদ্যাকে নিজের হাতের তুলি দিয়ে খেলা করতে পারতেন। এই ছিল ওঁর ভেতরে ডুব দিয়ে মণিমাণিক্য সংগ্রহের প্রধান উপায়। অতলে কী আছে তা তলিয়ে দেখা— তার নির্যাস সংগ্রহ করা। প্রয়োজনে ক্ষেত্রে প্রয়োগে ত্রুটি না রাখা। এখানেই তিনি আত্মদ্রষ্টা শিল্পী। শিল্পে যে বহিরঙ্গের সবকিছু লাগে না— লাগে তার সৌন্দর্যমণ্ডিত সুগন্ধটুকু। তাই এমন কথা বলাই সাজে শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের।
বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী নিয়ে দু-এক কথা বলে লেখা শেষ করতে চাই। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফাইন আর্টস বিভাগ খোলা হচ্ছে তখন। স্যর আশুতোষের ইচ্ছা অবনীন্দ্রনাথ তার কর্ণধার হন। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ তখন ঝাড়া হাত-পা। বই পড়া আর মনের আনন্দে ছবি আঁকা— মহানন্দে আছেন। কোনও ঝামেলাই নেই। মন তার আপন গতিতে চলেছে। স্যর আশুতোষ তাঁর প্রতিনিধি পাঠিয়েছেন, কিন্তু সকলকে নিরাশ করেছেন। আর চাকরিতে ধরা দিতে চান না। আর খাঁচার পাখি নয়। তিনি এখন মুক্ত বিহঙ্গ। মন যেদিকে যেতে চায় তাই চান তিনি। অগত্যা আশুতোষ স্বয়ং হাজির। ঘটনাটি ঘটেছিল ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে। অবনীন্দ্রনাথ আর চাকরিতে বাঁধা পড়তে নারাজ। কিন্তু আশুতোষ ছাড়বেন না। আশুতোষ বলেছিলেন— অবনবাবু, আপনি বছরে দুটো বক্তৃতা দেবেন, আমরা সকলে শুনে ধন্য হব। মাইনে নিয়ে কাজের কথা উঠতেই আশুতোষ বলেছিলেন— মাইনে নয়, ও তো অর্ঘ্য। অবনীন্দ্রনাথ স্যর আশুতোষের ব্যক্তিত্বের মাধুর্যে মুগ্ধ হযেছিলেন। স্যার আশুতোষের অনুরোধে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বাগেশ্বরী অধ্যাপক।
যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে বাগেশ্বরী বক্তৃতার প্রবন্ধগুলি পড়তেন, তখন প্রথম সারিতে থাকত ছাত্ররা, আর পেছনের সারিতে স্যর আশুতোষ প্রমুখ বিদ্বজ্জনেরা। এই বাগেশ্বরী প্রবন্ধমালা আট বছর ধরে অবনীন্দ্রনাথ বক্তৃতা দিয়েছেন। বহু মূল্যবান শিল্প-উপাদানে পরিপূর্ণ। বিশ্ববিদ্যালয় এই বক্তৃতামালা বই আকারে ছেপে বের করতে চেয়েছিল, বের হয়েছিল অনেক দেরিতে। মূল বাগেশ্বরী বক্তৃতাগুলি কেটেছেঁটে পুনর্লিখনের প্রয়োজন হয়েছিল। তার কারণ হিসাবে নিজেই লিখেছেন বইয়ের ভূমিকায়—‘যাত্রীতে যাত্রীতে পথ চলতে চলতে কথার মতো করে গাঁথা হয়েছিল এই সমস্ত প্রবন্ধ… যেমন খুশি যা খুশি বলে যাওয়া চলে সহযাত্রীদের মধ্যে বলেই যে সেগুলো সেইভাবেই পাঠকদের সামনে বই ছাপিয়ে প্রকাশ করতে হবে, তার কোনও কারণ দেখিনে।’
এখানেই কিছু কথা আমার মনে হয়, বক্তৃতার যে স্রোত তার ধরনধারণ আলাদা। সেই স্রোতে ভাসার যে আনন্দ, তাকে শুদ্ধিকরণে হৃদয়ে আবেগ অনেক কম হয়। শোনার যে আবেগে হৃদপদ্ম প্রস্ফুটিত হয়, তাকে হাতে রেখে পুজোর পদ্ম ফোটানো হলে, সে পদ্ম, পদ্মই থাকে না। আমি শিল্পী হিসেবে চাই আবেগে ভাসতে। গুটিপোকা তার গুটি কেটে যখন আকাশপানে ধায় তার রঙিন পাখায় আলোকরশ্মির যে বিচ্ছুরণ ঘটে, তাই মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে দেখতে চাই। ভোরের সূর্য ওঠাকে কাব্য করা যায় না। তাকে কেবলমাত্র হৃদয়ে ধরে রাখা যায়। এর বর্ণনার ভাষা নেই। তেমনই অবনীন্দ্রনাথকে লেখার মাধ্যমে পরিচয় দেওয়া যাবে না। যায় না। ইনি যে চিত্রকর।
শনিবারের চিঠি, ৫৩ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা