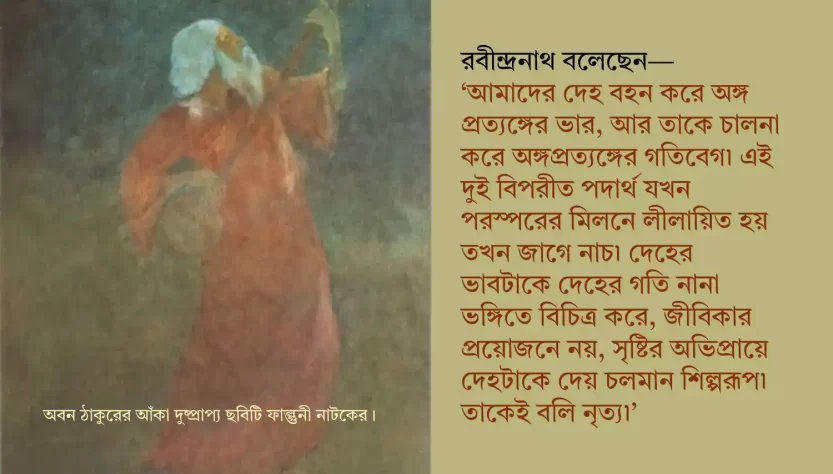ভারতীয় সংস্কৃতির একটি মূল্যবান এবং প্রাণবান শাখা নৃত্যকলা৷ প্রাক্-রবীন্দ্রযুগে নৃত্যের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায় নানান কারণে শিক্ষাভিমানী সম্প্রদায়ের কাছে নাচের কদর কমে গিয়েছিল৷ কলকাতায় তখন নাচ বলতে যা প্রচলিত ছিল, তা বাঈজি নাচের রূপান্তর মাত্র৷ এছাড়া সাধারণ লোকের মনোরঞ্জনে কুরুচিপূর্ণ নানান ধরনের নাচ— সঙের নাচ, ক্ষ্যামটা নাচ, জেলে-জেলেনির নাচ—মোটকথা কুরুচিকর দেহবিকৃতির নাচ দেখা যেত৷ নৃত্যের এই চরম অবক্ষয়ে নানান কাজের মধ্যেও নৃত্যকে শিল্পের মর্যাদায় অভিষিক্ত করার কথা প্রথম ভেবেছিলেন রবীন্দ্রনাথ৷ সেই সঙ্গে নাচকে বিশেষ মর্যাদায় শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে পবিত্র আসনে স্থাপন করেছেন তিনি৷ শান্তিনিকেতনে আত্মনিবেদনের অর্ঘ্য ‘নটীর পূজা’র শ্রীমতীর নৃত্য পরিকল্পনার প্রকাশ ও বিকাশ কারোর অজানা নয়৷
রবীন্দ্রনাথের নৃত্যভাবনা অনুধাবন করলে দেখা যায়, তাঁর গীতিনাট্য পর্ব থেকে নৃত্যনাট্য পর্বে উত্তরণের সময়কাল দীর্ঘায়িত৷ গীতনাট্য শুরু হয়েছে বাল্মীকি প্রতিভা দিয়ে ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে৷ এর পরে কালমৃগয়া, মায়ার খেলা, ঋতুরঙ্গ, নবীন, শ্রাবণগাথা, কবিতার সঙ্গে নাচ প্রভৃতি শান্তিনিকেতনে নানান কার্যক্রমে অনুষ্ঠিত হয়েছে৷ শান্তিনিকেতনের আশ্রমকন্যা অমিতা সেন বলেছেন, ‘মনে পড়ে ঋতুরঙ্গের মহড়া চলছে; কবি রচনা করলেন ‘শ্রাবণ তুমি বাতাসে কার আভাস পেলে’ এবং পরদিন উদয়নে গানের ভাবনৃত্য মেয়েদের দেখালেন; হাতের ভঙ্গিতে কদম ঝরে ঝরে পড়ছে, ‘হিমগিরি ফেলে নিচে নেমে এলে’— আগুন পোহানোর নাচ, কখনও বসে কখনও ঘুরে ঘুরে কখনও দাঁড়িয়ে—এরকম কত কত গানে নৃত্য শিক্ষার ছবি মনে গাঁথা হয়ে আছে৷’
১৯১২ সালে লেখা ‘ডাকঘর’ এবং ১৯১৬ সালে ‘ডাকঘরে’ গানের সংযোজন হয়েছিল৷ গান দুটি ‘ভেঙে মোর ঘরের চাবি’ ও ‘গ্রাম ছাড়া ওই রাঙামাটির পথ’৷ এই দুটি গানের সঙ্গে নাচের ভঙ্গিমা যোগ হল৷ নেচেছিলেন স্বর্গীয় যতীন্দ্রমোহন বসু এবং জাপানি মেয়ে ডোম্ফরা৷ শান্তিনিকেতনের নাচের উন্মেষ ও চর্চা কীভাবে ফল্গুধারার মতো চলেছিল সেকথা হয়তো বা সর্বজনবিদিত নয়৷
শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠার সূচনা হল ১৯০১৷ চার বছর পরে ১৯০৫ সালে কবি রচনা করলেন ‘সঙ্কোচের বিহ্বলতা’— গানটি৷ জুজুৎসু নাচের অনুকরণে কবির দৃষ্টিতে জাপানের পাঁচ আঙুলের খেলার সৌন্দর্যের সঙ্গে মিশ্রিত ছিল লীলাকৌশলের অসীম শক্তি৷ কবির একটি চিঠিতে দেখি,–‘এখানে জাপান হইতে জুজুৎসু শিক্ষক আসিয়াছেন। তাঁহার কাণ্ড কারখানা দেখিবার যোগ্য৷’ শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী তাঁর ‘স্বর্গের কাছাকাছি’ গ্রন্থে বলেছেন, ‘ঝুলন’ কবিতার নৃত্যরূপ আধুনিক ইউরোপীয় নৃত্যের আশ্রয়ে এবং ‘দুঃসময়’ মনিপুরী রীতিতে৷ রবীন্দ্রনাথের আবৃত্তির সঙ্গে নৃত্যের দুটি দৃশ্য আমার মনে গাঁথা হয়ে আছে৷’
রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—‘আমাদের দেহ বহন করে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ভার, আর তাকে চালনা করে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গতিবেগ৷ এই দুই বিপরীত পদার্থ যখন পরস্পরের মিলনে লীলায়িত হয় তখন জাগে নাচ৷ দেহের ভাবটাকে দেহের গতি নানা ভঙ্গিতে বিচিত্র করে, জীবিকার প্রয়োজনে নয়, সৃষ্টির অভিপ্রায়ে দেহটাকে দেয় চলমান শিল্পরূপ৷ তাকেই বলি নৃত্য৷’
কবির কণ্ঠে এই কবিতার সঙ্গে সৌমেন ঠাকুরের স্ত্রী শ্রীমতী হাতি সিং কালো কাপড়ের আচ্ছাদনের ভিতর থেকে তার কোমল পুষ্বনিভ মুখখানি তুলে একেবারে ঝড়ের বেগে স্টেজে এসে ঢুকলেন আর ‘তোমার কটি তটের ধটি কে দিল রাঙিয়া’— নেচেছিল দুটি ছোট ছোট মেয়ে৷ তার মধ্যে একজন কবির নাতনি নন্দিনী বা পুপেদিদি৷ মোমের পুতুলের মতো ছোট মেয়ে৷ এই নাচ সেদিনের বাংলার সকলকে ভারি আশ্চর্য করেছিল৷ এই ভাবেই শান্তিনিকেতন গানের সঙ্গে নাচের চর্চা চলেছিল৷ গীতিনাট্য থেকে নৃত্যনাট্য— পর্বটির সময়কাল দীর্ঘ৷
কবি শিশুতীর্থ এবং শাপমোচন রচনা করেছেন ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে৷ শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী লিখেছেন—“এই সময় ‘শিশুতীর্থ’ কবিতাকে আবৃত্তি সহযোগে নৃত্যরূপ দেওয়া হয়৷ শান্তিদেবকে আমরা নৃত্য করতে দেখেছি৷” প্রতিমা দেবীর একটি লেখায় দেখা যায় “শান্তিনিকেতনের বর্ষামঙ্গল উৎসবগুলির মধ্যে নৃত্যের প্রথম আকুতি দেখি… এল নটীর পূজার সরল ছন্দে নৃত্যের নূতন রূপ, সহজ স্নিগ্ধ তার গতি৷ …নটীর পূজার সঙ্গে শান্তিনিকেতনের সাজসজ্জা ও রঙ্গমঞ্চ বিশেষত্ব লাভ করেছিল৷… ঋতুরঙ্গে নাট্য সংযোজনা এবং সাজসজ্জার মধ্যে জাপানি স্থাপত্যের প্রভাব সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল৷” প্রতিমা দেবীর এই সব উক্তির মধ্যে একথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, রবীন্দ্রনাথ যা কিছু সুন্দর তাকে গ্রহণ করেছেন সৌন্দর্যবোধের চেতনায়৷
অধ্যাপক শংকরলাল মুখোপাধ্যায় বলেন, “রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভা স্বাঙ্গীকৃত হয়েছে এক অবিভাজ্য ছন্দময়তায়৷ কাব্যলোক থেকে সুরলোকে, সুরলোক থেকে রূপলোকে এবং শেষে রূপাতীত লোকে তাঁর শিল্পসত্তা সমুত্তীর্ণ হয়েছে৷ কবিতা থেকে গান, গান থেকে নাচে এসে শেষ বয়সে এক নতুন শিল্পরূপের প্রকাশ ঘটালেন৷ তাঁর শেষ বয়সে রচিত নৃত্যনাট্যগুলি— চিত্রাঙ্গদা, চণ্ডালিকা এবং শ্যামা নাচে গানে, দৃশ্য সজ্জায় সকলকে বিমোহিত করে৷ শান্তিনিকেতনে তিনি যে নাচের প্রচলন করেছেন তাকে কেউ বলেছেন শান্তিনিকেতনের নাচ, কেউ বা বললেন, Tagore School of Dance, আবার কারোর মতে এ হল ইম্প্রেশনিস্ট ধরনের নাচ৷” তবে বলা যেতে পারে, ভারতীয় নৃত্যের প্রতি গভীর চিন্তা এবং অনুরাগবশত রক্ষণশীল প্রথাবদ্ধ নৃত্যধারায় প্রথম মুক্তি আনলেন রবীন্দ্রনাথ এবং তিনি এক অভিনব সৌন্দর্যমণ্ডিত নৃত্যধারারও প্রবর্তন করলেন৷ ধ্রুপদী ও আঞ্চলিক নাচের নির্যাসটুকু গ্রহণ করে ভাবে গাম্ভীর্যে, রসের মাধুর্যে, নান্দনিক বিশুদ্ধতায় এই নৃত্য হল এক অভিনব সৃষ্টি৷
“রবীন্দ্রনৃত্যে একদিকে রয়েছে ভারতীয় ধ্রুপদী নাচের আঙ্গিক প্রকরণসহ নৃত্যাভিনয় পদ্ধতির আভাস, সঙ্গে আছে আঞ্চলিক লোকনৃত্য ও বিদেশি নৃত্যের পরোক্ষ নির্যাস৷ নৃত্যাভিনয়ে দক্ষিণী কথাকলি নাচের আঙ্গিক ব্যবহার করেছেন কিন্তু কথাকলির রূপসজ্জা (Make up) পোশাক এবং মুদ্রাভিনয় বর্জন করেছেন৷ তেমনি মনিপুরী নাচের লাবণ্যপূর্ণ আঙ্গিককে গ্রহণ করেছেন কিন্তু পোশাক বা তালবাদ্যের জটিলতার ব্যবহার থেকে বিরত থেকেছেন৷ প্রচলিত নৃত্যধারার গণ্ডি ভেঙে তিনি নতুন ধারার সৃষ্টি করেছেন৷ রবীন্দ্রনৃত্যধারার এই স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য ভারতীয় নৃত্যধারায় সৃষ্টিশীলতায় পথ খুলে দিয়েছে৷ নৃত্যশীল যে ভারতীয় নৃত্যকলা, ধ্রুপদী আঙ্গিকের কঠিন শাসনের জটাজালে আবদ্ধ ছিল তিনি তাকে ভগীরথের মতো মুক্ত করে এক নতুন ধারার মন্দাকিনীর সৃষ্টি করেছেন৷”
রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য রচনায় তাঁর বিদেশ ভ্রমণের পরোক্ষ প্রভাব রয়েছে৷ যেমন জাপানের প্রাচীন নাট্যকলা নো (Noh) এবং কাবুকি (Kabuki) নাচ৷ জাভা এবং বলদ্বীপের বিভিন্ন ধরনের ওয়েগাঙ (Wayang) নাচ, সিংহলের কাণ্ডী, ইউরোপের ব্যালে ইত্যাদির প্রভাব রবীন্দ্রসৃষ্ট নৃত্যধারায় সুস্পষ্ট৷ এই নৃত্যশৈলীতে রক্ষণশীলতার সে রকম পরিচয় না থাকলেও, রবীন্দ্রনৃত্যের মূল লক্ষ্য গানের ও নাট্যভাবের অন্তর্নিহিত ভাবরস নৃত্যের মাধ্যমে প্রকাশ করা তা যে কোনও আঙ্গিকের সহায়ে হোক৷ রবীন্দ্রনৃত্যের মূল কথা ছন্দোময়তা এবং শেষ কথা রসসৃষ্টি৷
রবীন্দ্রনৃত্য চিন্তাধারার অনুকরণে আমরা ‘জাপান যাত্রী’তে দেখি,– ‘একদিন জাপানি নাচ দেখে এলুম৷ মনে হল এ যেন দেহভঙ্গির সংগীত৷ এই সংগীত আমাদের দেশে বীণার আলাপন অর্থাৎ পদে পদে মিড়৷ ভঙ্গি বৈচিত্রের পরম্পরায় মাঝখানে কোনও ফাঁক নেই কিংবা কোথাও জোনের চিহ্ন দেখা যায় না৷ সমস্ত দেহ পুষ্পিত লতার মতো এক সঙ্গে দুলতে দুলতে সৌন্দর্যের পুষ্পবৃষ্টি করছে৷ খাঁটি ইউরোপীয় নাচ অর্ধনারীশ্বরের মতো—আধখানা ব্যায়াম, আধখানা নাচ, তার মধ্যে লম্ফ ঝম্ফ ঘুরপাক আকাশকে লক্ষ করে লাঠি ছোঁড়াছুঁড়ি আছে৷ জাপানি নাচ একেবারে পরিপূর্ণ নাচ৷ দেহসজ্জার মধ্যে লেশমাত্র উলঙ্গতা নেই— এই বোধ হয় যে সৌন্দর্যপ্রিয়তা জাপানির মনে এমন সত্য যে তার মধ্যে কোনরকমের মিশেল তাদের দরকার হয় না৷’
রবীন্দ্রনাথ নিজে বলেছেন, আমি মূলত কবি৷ কিন্তু তাঁর কবিত্ব ছাপিয়ে ভিন্নমুখী প্রতিভার বিকাশে আমরা দেখি,– তিনি সুরকার, নাট্যকার, চিত্রকর, অভিনেতা, সঙ্গীতকার, রূপকার এবং সর্বোপরি ভারতীয় নবনৃত্য আন্দোলনের উদ্গাতা ও নবভারতীয় নৃত্যধারার পথিকৃৎ৷ ভারতীয় নৃত্যের পুনরুজ্জীবনে সমাজে তার সম্মানজনক প্রতিষ্ঠায় তিনি পুরোধা৷ শাস্ত্রীয় প্রকরণের জটিলতার থেকে নৃত্যধারাকে সৃষ্টিশীল নব নব পথে প্রবাহিত করেছেন৷ এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—‘আমাদের দেহ বহন করে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ভার, আর তাকে চালনা করে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গতিবেগ৷ এই দুই বিপরীত পদার্থ যখন পরস্পরের মিলনে লীলায়িত হয় তখন জাগে নাচ৷ দেহের ভাবটাকে দেহের গতি নানা ভঙ্গিতে বিচিত্র করে, জীবিকার প্রয়োজনে নয়, সৃষ্টির অভিপ্রায়ে দেহটাকে দেয় চলমান শিল্পরূপ৷ তাকেই বলি নৃত্য৷’
আসলে রবীন্দ্রনাথ একদা সমাজের নিন্দিত অবস্থান থেকে নৃত্যকে মুক্ত করে জীবনের অঙ্গরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন৷ তারই ধারা বহন করে সৃষ্টিশীল ভারতীয় নৃত্য, গুরু উদয়শঙ্করের পথ ধরে আজ বিশ্বসভায় আসন করে নিয়েছে৷ ভারতের সৃষ্টিশীল নৃত্যধারায় উদয়শঙ্কর যদি বহির্বিশ্বে তার উজ্জ্বল প্রকাশ ঘটিয়ে থাকেন তাহলে রবীন্দ্রনাথ তার ভিত্তিভূমি রচনা করেছেন শান্তিনিকেতনের নিভৃত পরিসরে৷
নৃত্যের এই সংজ্ঞাই রবীন্দ্রনাথের নৃত্যভাবনাকে প্রণোদিত করেছে৷ রবীন্দ্রসঙ্গীতের ছন্দিত আন্দোলনে নৃত্যশিল্পী গানের ভাব ও ভাবনাকে প্রকাশ করে, –এই ছন্দ এবং ভাবনা রবীন্দ্র চিন্তার বিরুদ্ধে যেন না যায়৷ রবীন্দ্রনাথের একটি মন্তব্য এই প্রসঙ্গে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য৷ তিনি বললেন—‘মাথায় জলপূর্ণ কলস লইয়া নৃত্য করা যেরূপ— হাজার অঙ্গভঙ্গি করিলেও এক বিন্দু জল উথলিয়া পড়িবে না, ইহাও সেইরূপ একপ্রকার কষ্টসাধ্য ব্যায়াম৷ সহজ ও স্বাভাবিক নৃত্যের যে একটি শ্রী আছে ইহাতে তাহার যেন ব্যাঘাত করে৷ ইহাতে কৌশল প্রকাশ করে মাত্র৷ নৃত্যের পক্ষে কি ইহা স্বাভাবিক, না তাহা নৃত্যের উদ্দেশ্যসাধন করে? নৃত্যের উদ্দেশ্য কী? না অঙ্গভঙ্গির সৌন্দর্যে অঙ্গভঙ্গির সৌন্দর্যে কবিতা দেখাইয়া মনোহরণ করা৷ সে উদ্দেশ্যের বহির্ভূত যাহাকিছু তাহা নৃত্যের বহির্ভূত। তাহাকে নৃত্য বলিব না৷ তাহার অন্য নাম দিব৷’
রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং নাচে অংশ নিতেন। অন্যদেরও নাচিয়ে ছাড়তেন। এমনটা প্রত্যক্ষ করেছেন শান্তিনিকেতনের প্রবীণ আশ্রমিকরা। প্রত্যক্ষদর্শী সুধীর কর লিখছেন – যেবার রাজা অভিনয়ের মহড়া চলছে উত্তরায়ণে, দিনের পর দিন সন্ধ্যায় সকলকে পাঠ শেখানো, সকলের সঙ্গে গান গাওয়া ছিল তাঁর নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। পথিকদের দৃশ্য এলেই অভিনেতাদের বলতেন, ‘শুধু গাইলে হবে না, নাচতে হবে।’ দলের দু-একজন নাচে স্বাভাবিক পটু ছিলেন, কিন্তু বাদবাকি আনাড়িদের আড়ষ্টতা দেখে তিনিও আসন ছেড়ে উঠে পড়তেন, নেচে দেখাতে লাগতেন – গ্রামের লোকের উত্সবের নাচ। শেষে সকলকে নিয়ে নৃত্যে-গীতে মাতিয়ে তুলতেন। ‘ঠাকুরদা’ হয়ে নেচে নেচে গাইতেন- ‘যা ছিল কালো ধলো/(তোমার) রঙে রঙে রাঙা হল…।’
রবীন্দ্রনাথের নৃত্য ভাবনার মূল সুর ছিল, ভারতীয় ঐতিহ্যে একটি নূতন ধারার নৃত্য সৃষ্টি করা৷ তাই তিনি শান্তিনিকেতনে লক্ষ রাখতেন কোন ধরনের আঙ্গিক কোন চরিত্রে উপযোগী হবে এবং সেদিকে সচেতন হয়ে নৃত্য সমাবেশ করতেন৷ এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিমা দেবী বলেছেন, ‘ভিন্ন ভিন্ন খণ্ড নাচ মিলে ক্রমে ক্রমে যে এমনি করে একটি সম্পূর্ণ ভূমিকা পরিণত হতে পারে তারই নতুন পদ্ধতি চোখে পড়তে লাগল৷ নীচের ক্লাসগুলি দেখতে গিয়ে বুঝতে পারলুম মনিপুরী ও দক্ষিণী নাচের অনেক ভঙ্গি ও তাল একটার সঙ্গে একটা জুড়ে দিলে একটি ভূমিকা অনায়াসেই তৈরি করা যায়৷’
ভারতীয় নৃত্যের পুনরুজ্জীবন ও নবধারার নির্মাণে রবীন্দ্রনাথের অবদান অপরিমেয়৷ তাঁর প্রবর্তিত নৃত্যধারার ইতিহাস অনুধাবন করলে সহজেই বোঝা যায় নৃত্য তাঁর কাছে ছিল পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার অঙ্গ৷ এই প্রসঙ্গে গুরু শান্তিদেব ঘোষ বলেন, শিক্ষাক্রমে এই নৃত্য শুধু শিক্ষাতিরিক্ত (Extra curricular) ছিল না, ছিল শিক্ষাসম্পৃক্ত (Cocurricular)৷ তাই পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাদর্শে সঙ্গীত ও নৃত্যকে স্থান দিলেন অন্যান্য শিক্ষার সঙ্গে একই পাঠক্রমে৷ এরই ফল আমরা দেখি যে বাংলায় অচিরেই শিক্ষিত পরিবারের ছেলেমেয়েরা এবং বধূরা সসম্মানে নৃত্যের চর্চা করতে পারছেন অবাধে৷ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠক্রমে নৃত্যের বিষয়ে শিক্ষা ও গবেষণার সুযোগ হয়েছে অবারিত এবং তারও মূলে রয়েছে রবীন্দ্রনাথ৷
আসলে রবীন্দ্রনাথ একদা সমাজের নিন্দিত অবস্থান থেকে নৃত্যকে মুক্ত করে জীবনের অঙ্গরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন৷ তারই ধারা বহন করে সৃষ্টিশীল ভারতীয় নৃত্য, গুরু উদয়শঙ্করের পথ ধরে আজ বিশ্বসভায় আসন করে নিয়েছে৷ ভারতের সৃষ্টিশীল নৃত্যধারায় উদয়শঙ্কর যদি বহির্বিশ্বে তার উজ্জ্বল প্রকাশ ঘটিয়ে থাকেন তাহলে রবীন্দ্রনাথ তার ভিত্তিভূমি রচনা করেছেন শান্তিনিকেতনের নিভৃত পরিসরে৷ সেদিনের সেই রবীন্দ্ররোপিত বীজই আজ এক বিরাট মহীরূপে পরিণত হয়েছে ও নব নব সৃষ্টিধারায় ভারতীয় নৃত্যকে পরিপুষ্ট করে চলেছে৷