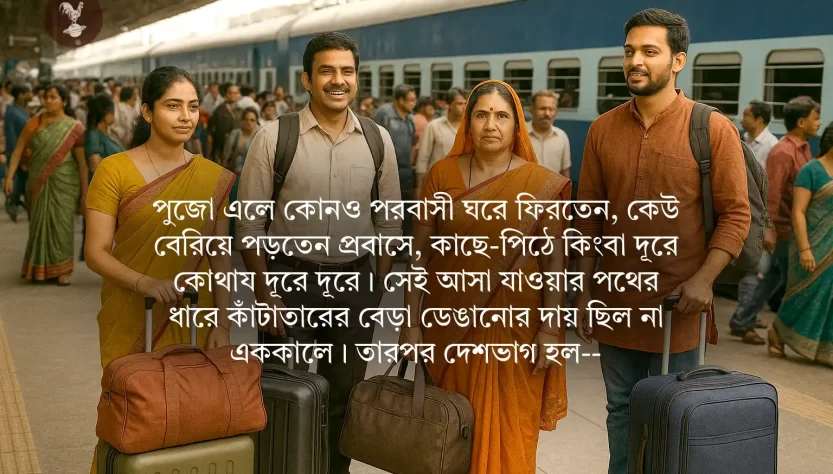বাঙালির তো পায়ের তলায় সর্ষে। আর পুজো এলেই মন উড়ু উড়ু। এই ঐতিহ্য কয়েক শতাব্দীর। মানে যখন অবিভক্ত বাংলা ছিল, তখন থেকেই। পুজো এলে কোনও পরবাসী ঘরে ফিরতেন, কেউ বেরিয়ে পড়তেন প্রবাসে, কাছে-পিঠে কিংবা দূরে কোথায দূরে দূরে। সেই আসা যাওয়ার পথের ধারে কাঁটাতারের বেড়া ডেঙানোর দায় ছিল না এককালে। তারপর দেশভাগ হল– রেলপথের বিস্তারে বাঙালির পুজোয় ভ্রমণের মানচিত্র, ভ্রাম্যবিলাসের ধরনধারণও গেল বদলে, তা-ই ফুটে উঠেছে প্রতিবেদকের কলমে।
…ঢাকের কাঠির নরম বোলে
পুজো আবার এল চলে
শিউলি, শালুক, আগমনীর সুরে।
ঘর ডেকে কয় আয়রে কাছে
বছর-পরে সবার মাঝে
বাহির ডাকে দূরে-অনেক দূরে।…
বাংলার দুর্গাপুজো মানে বাঙালির ঘরে ফেরা কিংবা ঘর থেকে পালানো, দূরে– অন্য কোথাও। রুজির তাগিদে যেজন রয়েছে পরবাসে, ভিটে মাটি শেকড়ের টানে বছর শেষে ঘরে ফেরার আনন্দ যে কী, সেজনই জানে। আবার ঘর পালানোর ফুরসত তো ‘ঢ্যাং কুড়াকুড়— ঢ্যাং কুড়াকুড়’ বাদ্যি বাজলেই তেমন ভাবে মেলে। আর ঘরে ফেরা বা পালানোর মানে হলো রেলগাড়ির ঝমাঝম। কারণ কু-ঝিক-ঝিক-এর দিন তো সেই কবেই কাশবনের মাথা ছুঁয়ে পদ্মপুকুরের জেল ঢেউ তুলে শরতের নীলে হারিয়ে গেছে। বাস-ট্রামের প্যাঁ-পোঁ আর এরোপ্লেনের মাথার উপর দিয়ে হুস করে উড়ে যাওয়া। সহজপাঠের কথা মনে আছে? তার দ্বিতীয়ভাগের সেই ঘুম ঘুম কবিতাগুলো? রবিঠাকুর তার শব্দে ও ছন্দে পুজোর ছুটিতে ঘরে ফেরার ছবি এঁকেছেন—‘স্টিমার আসিছে ঘাটে পড়ে আসে বেলা, পুজোর ছুটির দল লোকজন মেলা।’ সেটা ছিল ১৯৩০ সাল। এর মধে: গঙ্গা-পদ্মা দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে, হারিয়ে গেছে রবিঠাকুরের দিন। তাঁর সেই কালজয়ী লেখা দেশভাগের ছুরিকাঘাতে ছিন্ন। প্রকৃতির খেয়ালিপনা আর মানুষের অবিবেচনায় নদীর পথ গিয়েছে হারিয়ে। তাই সে কবিতা এখন শিশুপাঠের অলীক কল্পনা আর বনদের মন কেমন করা হলদে হয়ে যাওয়া অতীত।
সবারই এরকম মন কেমন করা কিছু না কিছু আগমনীর স্মৃতি মনের মাঝে তন্দ্রাচ্ছন্ন থেকে যায়। ছুটির অবকাশে তারই কয়েকটা রোমন্থন করলে মন্দ হয় না। আমাদের বসন্তদাদু ছিলেন বউবাজারের পোস্টমাস্টার, বাড়ি ময়মনসিংহের শিমুলকান্দি গ্রামে। বৈঠকখানা বাজার থেকে শাড়ি, ধুতি, জামাকাপড় আর চিনাবাজার থেকে চটিজুতো কিনে গাঁটরি বাঁধতেন। টিনের তোরঙ্গে থাকত নানা জনের নানান প্রয়োজনী ও আবদারের মনোহারী দ্রব্য। চতুর্থীর দিন সন্ধ্যায় শিয়ালদা (তখনকার কলকাতা)স্টেশন থেকে চড়ে বসতেন গোয়ালন্দ মেলে, ইন্টারক্লাসের কাঠের বেঞ্চে লটবহরের পশরা সাজিয়ে। গাড়ি চলত সারারাত। সকাল হত গোয়ালন্দ ঘাটে। তারপর স্টিমারে পদ্মা পার হয়ে মাণিকগঞ্জ। সেখান থেকে আবার ট্রেন ধরে মেঘনার তীরে ভৈরব বাজার। নদীর সেখানে আদিগন্ত বিস্তার আর ছোট্ট পানসি নৌকায় করে মেঘনা পারাপার। তারপর কোদালকাঠি খালের উজান বেয়ে শিমুলকান্দি পৌঁছতে পৌঁছতে মহাষষ্ঠীর সন্ধ্যা। শুধু নিজেদের বাড়িতে নয়, সারা পাড়ায় সাড়া পড়ে যেত—‘বসন্ত এসেছে।’ বামুনপাড়ার ঘোষালবুড়ি তার ভাঙা কোমর নিয়ে টুকটুক করে এসে এক গাল হেসে বলত, ‘বসন্ত এসেছিঠস বাবা?’ কাপড়ের গাঁটরি থেকে একটা সাদা থান বার করে প্রণাম করতেন দাদু। ঘোষালবুড়ি থান হাতে আশীর্বাদ করতেন—‘বেঁচে থাকো বাবা, শতায়ু হও।’ বসন্তদাদুর কপালে শেষ পর্যন্ত পেনশন জোটেনি তবে বহু মৃত্যুর দর্শক হয়ে ঘোষালবুড়ি একশো পার করেছিলেন।
পুতুলমাসির মুখে শুনেছি কোনও কোনও বার পুজোতে বিদ্যাকূট থেকে শিবনাথদাদু নৌকো পাঠিয়ে দিতেন ভাগ্নাভাগ্নিদের মামাবাড়ি নিয়ে যেতে। ধানখেতের মধ্যে দিয়ে খাল, তারপর তিতাস-কালিন্দীর ধারা বেয়ে বিদ্যাকূট। সঙ্গে আসত চিনু মাঝিআর গোবিন্দ লেঠেল। বিদ্যাকূটের একান্নবর্তী পরিবারে বড় মেজো আর ছোট তরফের পুজোর ভার পড়ত পালা করে। মেজো তরফের শিবনাথদাদু একটু বেশিই খরুচে। তাঁর পালায় মা-মাসিদের গায়ে তাঁতের বদলে জামদানি শাড়ি উঠত। মেজোদাদুর জীবদ্দশাতেই শুনেছি রায়চৌধুরী পরিবারের দুর্গাপুজোর চাকচিক্য তিতাস-কালিন্দীর ধারার মতোই মজে আসে।
আমার দিদিমার বাপের বাড়ি ছিল যশোর জেলার উত্তরডিহি গ্রামে। গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে যেত ভৈরব নদ। উত্তরডিহির তিন মাইল দক্ষিণে দক্ষিণডিহি গ্রামে রবীন্দ্রজায়া ভবতারিণীর (ঠাকুরবাড়ি আসার পর তাঁর নাম হয়েছিল মৃণালিনীদেবী) বাপের বাড়ি। সেই সূত্রে রবিঠাকুর ছিলেন পাশের গ্রামের জামাই, গর্ব করার মতো বিষয় বটে। আর দিদিমা সেই কথা প্রায়ই বলতেন। শিয়ালদা থেকে যশোর যাওয়ার কোনও হ্যাপা ছিল না। সোজা ট্রেনেই যাওয়া যেত। তাই রাণু, বেলাদের বোধ করি মামাবাড়ি যেতে জল-কাদা ভাঙতে হতো না। রবীন্দ্রনাথকেও সোনালি জরির কাজ করা নাগরা জুতো বগলে নিয়ে পরনের ধুতি সামলাতে নাজেহাল হতে হয়নি। তবে আমার দাদু একবার দিদিমাকে নিয়ে উত্তরডিহি গিয়েছিলেন বিয়ের পরে পরে। মেয়েদের তেমন জুতো পরার চল ছিল না সে সময়ে। পুজোর তত্ত্বে পাওয়া নতুন জুতো হাতে নিয়ে নতুন জামাই হাজির শ্বশুরবাড়ির দরজায়। কারণ ফোস্কা পড়া পায়ে শুষ্ক কোলাপুরী চটি পরার থেকে খালি পায়ে ১২ মাইল মেঠো পথ হাঁটা অনেক সহজ। এখন আর কেউ ট্রেন থেকে স্টিমার, স্টিমার থেকে নৌকো, নৌকো থেকে গরুর গাড়ি, গরুরগাড়ি থেকে নেমে পায়ে হেঁটে বাড়ি ফেরে না। পূর্ব বাংলা এখন আলাদা রাষ্ট্র, নদীনালাগুলোও শুনি শুকিয়ে গেছে। চাষিরা জুলি ধান কাটে বটে, তবে ডিঙি চড়ে সারিগান গেয়ে ঘরে ফেরে না।
শারদীয়ার ভ্রমণ বাঙালির কাছে একটা বিশেষ মাত্রার। কবে থেকে, কীভাবে, কোথায় এর সূচনা তার উত্তর সাহিত্যে, ইতিহাসে, ভ্রমণকারীর যাত্রাপথের মাইলস্টোন থেকে জানতে পারা যায় না। জানার প্রয়োজনও নেই। বাঙালি শুধু এটুকুই জানে যে পদ্ম ফোটার সময় হলে, রোদ্দুরে কাঁচা হলুদের রং লাগলে বেরিয়ে পড়তে হয়। বেরিয়ে পড়তে হয় চেনা গণ্ডির বাইরে, নীল আকাশে মেঘের ভেলায় ভেসে। না হলে প্রতিদিনের থোড়-বড়ি-খাড়া আর খাড়া-বড়ি-থোড় আমাদের অন্তরাত্মা হাঁফিয়ে ওঠে। ভ্রমণের উদ্দেশ্য তো শুধু দেশ পরিচয় নয়, মানুষজনকে জানাও নয়। ভ্রমণ প্রকৃতির পাঠশালায় জীবনের সহজপাঠ।
পশ্চিমবঙ্গে যে এমন নদীনালা কখনও ছিল না। কাজেই হাওড়া বা শিয়ালদা থেকে ট্রেনে চড়ে নিজের স্টেশনে নেমে, মাথায় ছই দেওয়া গরুরগাড়ি চেপে, কী পায়ে হেঁটে ফিরতে হতো নিজের গ্রামে। এখন যতই ছোট স্টেশন বা হল্ট হোক না কেন, ভ্যানরিক্সা বা ট্রেকার মেলে। বর্ধমান থেকে রামপুরহাটের দিকে যে লুপলাইনটা চলে গেছে সে পথে পড়ে পিচকুড়ির ঢাল, বলপাস, নোয়াদার ঢাল এরকম ছোট ছোট স্টেশন। রেললাইনের দু’দিকে অবারিত মাঠ। দেখি যাত্রীরা ট্রেন থেকে নেমে পিঠে মাথায় বোঁচকা-বুঁচকি নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হারিয়ে যায় দিগন্তে সোনাঝুরি, আকাশমণি গাছেদের আড়ালে। সার বেঁধে সকালে দ্রুত চলে। পায়ে তাদের বছর পরে ঘরে ফেরার ছটফটানি তার মাথার বোঝায় নতুন কাপড়ের গন্ধ। মফস্বলের স্টেশনের পাশেই দাঁড়িয়ে থাকে বাস। সে বাসে ভেতরে যতজন না বসে ছাদে চড়ে তার অনেক বেশি।
এরকম এক অভিজ্ঞতার কথা বলি। সেবারে পুজোয় হাসিদির বাড়ি গিয়েছিলাম, বাঁকুড়ার লোকপুরে। আশুদা তখন মেডিকেল কলেজে চাকুরে। সেটাই আমার কলেজ বয়সে প্রথম একলা চলার স্বাধীনতা। দুর্গাপুরে ট্রেন থেকে নেমে চড়ে বসলাম বাঁকুড়ার বাসে। তিল ধারণের স্থান নেই, ঘরে ফেরার ভিড়। কেউ বসে, কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ বা বাসের ছাদে। জানালা দিয়ে ডিভিসি ব্যারেজের জল দেখে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলাম না। পরের স্টপেজেই ঠেলেঠুলে জায়গা করে নিলাম বাসের মাথায়। তারপর চলন্ত বাসের মাথায় বসে খেয়ালি মেঘের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলা। দামাল বাতাসে শিশিরে ভেজা কদম, ছাতিমের গন্ধ। ভগবান গলায় সুর দেননি, তবু হেঁড়ে গলায় প্রাণ খুলে গাইতে লাগলাম—‘আমার মুক্তি আলোয় আলোয়, এই আকাশে।‘ মাণিক মাহাতো পুজোর ছুটিতে বাড়ি ফিরছেন, বেলিয়াতোড়ে। আঙুল দিয়ে দূরে শালে বন দেখিয়ে বলে—‘ওই হলো বাঁধকানার জঙ্গল, এ সময় বুনো হাতিদের আড্ডা। আঁধার নামলে দলে দলে চলে আসে লোকালয়ে, চাষের ক্ষেতে ধানের থোড় খেতে। সুযোগ পেলে দুর্গামণ্ডপ থেকে কলাবউকেও হরণ করে নেয়। কোনও কোনও বার মা আসেন হাতিতে চড়ে। আবার সেই হাতিই দল বেঁধে তছনছ করে দিয়ে যায় প্রতিমাসহ দুর্গামণ্ডপ। হুলো-পার্টির লোকজন এসে টিন পিটিয়ে জ্বলন্ত মশাল ছুড়ে হাতি খেদায়। বুনো হাতি যে কী জিনিস ভাবতে পারবে না। সিংহও তার ভয়ে মিউ মিউ করতে থাকে।
পুজোয় দার্জিলিং আর দার্জিলিং-এর টয় ট্রেন— তাকে নিয়ে কত না গল্প আর কত না কবিতা। আপনারা অনেকেই সেই ট্রেনের যাত্রী হয়েছেন। কিন্তু জানেন কি, পশ্চিমবঙ্গে অনেক দিন পর্যন্ত কু-ঝিক-ঝিক করে ছোটলাইনের (ন্যারোগেজ) ট্রেনগাড়ি চলত? আহম্মদপুর থেকে কাটোয়ার দিকে। ব্রডেগেজের নিছক গদ্যের দাপটে আজও সেই রেলগাড়ি ছিল একাই নিজের ছন্দ, মাত্রা, গতিতে শেষের কবিতা হয়ে টিকে আছে এই বাংলায়। একবার শুধু শখ করে আহম্মদপুর থেকে এই ট্রেনে চড়েছি, গন্তব্য বলে কিছু ছিল না। রেলগাড়ির জানালা দিয়ে দেখা ‘মহা ভাদরের মহবা বাদরে’ বাংলার ঢল ঢল মুখ। রেললাইনের দু’ধার নাবাল জমি, তারপর সবুজ ক্ষেত, ক্ষেত পেরিয়ে মাঠপুকুর, পুকুরের উঁচু পাড়ে তাল-খেজুরের জটলা। রাঙামাটির রাস্তায় লোক চলেছে হেঁটে, সাইকেলে, জল-কাদা ছিটিয়ে মোটর-বাইকে। ট্রেন থামছে মাঠের মাঝে, কখনও বা গ্রামের ধার ঘেঁষে। যাত্রী নামছে, উঠছে, প্ল্যাটফর্ম বলে কিছু নেই, লাল মোরাম বিছানো। দু-একটা তেলের বাতি, এক কামরার টিকিট ঘর। একজন মাত্র কর্মী । সে সবুজপতাকা নাড়ে, বাঁশিতে ফুঁ দেয়। গাড়ির গতি ধীরে ধীরে কমে আসে। জানলার বাইরে গ্রাম বাংলার মুখ। কয়েকটা কোঠাবাড়ি, পরিপাটি করে নিকোনো উঠোন, ধানের মরাই, ছাইগাদায় ব্যস্ত মুরগি। তারপর পানাডোবা, খিড়কির দরজায় অপেক্ষায় কেউ। তারপর হঠাৎই তেঁতুলগাছে বাঁধা মাইক, তাতে হিন্দিগানের ডপলার এফেক্ট।
মা দুর্গা ছেলেমেয়েদের নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন অতি সাধারণ, ‘না-থিমের’ এক প্যান্ডেলে। সামনে চৌহাট্টা স্টেশনে নামবে বলে এক বুড়ি পোঁটলা-পুঁটলি গুছিয়ে দরজার কাছে। জিজ্ঞাসা করি, ‘কী মাসি, বাড়ি কোথায়?’ ফোকলা গালে একমুখ হেসে বলে, ‘হুই জি বাজপড়া তালের গাছ লি লি কইরছে, উর পেছনে আমাদের গেরাম। লাতিন দু’টর লেগে পুজয় নতুন জামা কিনে লিঙে যেছি। আমায় অ’রা খুব মানে গো।’
ওদিকে ঘোড়াগাড়ির তেমন চল ছিল না। এক্কাগাড়ির দেখা মিলত বিহার সংলগ্ন রাঢ় বাংলায় আর মুর্শিদাবাদে। খুব ছোটবেলায় পুজোর ছুটিতে একবার পিসির বাড়ি গিয়েছিলাম সাঁওতাল পরগনায়। সাহেবগঞ্জ লোকাল যখন বার হাড়োয়া স্টেশনে থামল, বিকেল তখন ঢলে পড়েছে। ঘোড়ার গাড়িতে যেতে যেতে দেখি ঢেউ খেলানো পাহাড়ের পিছনে সিঁদুরে সূর্যটার লুকোচুরি খেলা। কালাবাড়িতে যখন নামলাম আঁধার নেমেছে ঘন হয়ে। পিসেমশাই দেখি হ্যারিকেন হাতে দাঁড়িয়ে আছেন গরুর গাড়ির সামনে। তখনও ওদিকে বিজলিবাতি আসেনি। অন্ধকারে গাড়ি চলেছে হেলেদুলে, কাঁচোর-ম্যাঁচোর। বলদ দুটোর সঙ্গে গাড়োয়ানের ‘হই হই, লিক লিক, হু-র-র-র-হ্যাঁ—’ সে কত কথা। ছই-এর নচে ঝোলানো লণ্ঠনের আলোয় কাঁচা রাস্তার খানাখন্দ আর প্রতিটা বাঁক রহস্যময় লাগছিল। আঁধারে কিছুই ঠাওর হয় না। তবে গন্ধে বোঝা যায় কোন ক্ষেতটা খেসারির আর কোনটায় ছোলা ফলেছে। আতাপুর পার হতেই উঠল চতুর্থীর চাঁদ। রাস্তার উপর হেলা বটগাছটা গায়ে ফিনফিনে কুয়াশার সাদা থান পরে অশরীরীর মতো দাঁড়িয়ে আছে। জায়গাটার বদনাম আছে। নীচ দিয়ে যেতেই ডালপালায় ঘুমিয়ে থাকা পাখপাখালিরা জেগে উঠল। আর তাদের কর্কশ ডাকে পেটের ভেতরটা কেমন যেন গুরগুর করে উঠল। রাস্তার ডানদিকে বিশাল ঠাকরুণ-পোঁতা বিল। আমি অনেককে জিজ্ঞাসা করেছি এই ঠাকরুন কে ছিল, আরতাকে কেনই বা পোঁতা হয়েছিল। স্থানীয় কারও কাছে জবাব পাইনি। ভাঙা চাঁদের আলো বিলের জলে বিলি কাটছে আর তার সঙ্গে কাশবনের মাথা নাড়া। এ যেন সেই পৃথিবীই নয়। মনের ভয়ের সঙ্গে মিশে ছিল চোখের ভালো লাগা। ছই-এর ফাটল গলে তারারা নেমে এসেছিল ঘুমপাড়ানি গল্প বলতে। কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না। দাদা-দিদির ডাকে জেগে উঠে দেখি পৌঁছে গেছি ন’পাড়ায়। নির্জন দুর্গাতলায় মা দুর্গা তখন দো-মেটে দিগম্বরী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।
ড্যাঞ্চিবাবুকাদের বলে মনে আছে? বাঙালি যারা শুধু খেতে, ঘুমোতে আর খাওয়ার গল্প করতে পশ্চিমে পাড়ি দিতেন, স্থানীয় হিন্দিভাষীরা তাদের ড্যাঞ্চিবাবু বলত। দেহাতি হাটে তারা গাদা গাদা শাকসবজি, গণ্ডা গণ্ডা দেশি মুরগি, ডজন ডজন মুরগির ডিম, নধর ছাগলছানা কিনে মুটের মাথায় চাপিয়ে বাসায় ফিরতে ফিরতে সঙ্গী অপর কোনও বাঙালিবাবুকে গদগদ স্বরে বলতেন, মশাই, বুইলেন কিনা, এখানে সবই ড্যাম চিপ। এই ড্যাম চিপ থেকেই ড্যাঞ্চিবাবু। সেই ড্যাঞ্চিবাবুরা হারিয়ে গেছে, হারিয়ে গেছে পশ্চিমের হাওয়া-বদলের অলস দিন।
শারদীয়ার ভ্রমণ বাঙালির কাছে একটা বিশেষ মাত্রার। কবে থেকে, কীভাবে, কোথায় এর সূচনা তার উত্তর সাহিত্যে, ইতিহাসে, ভ্রমণকারীর যাত্রাপথের মাইলস্টোন থেকে জানতে পারা যায় না। জানার প্রয়োজনও নেই। বাঙালি শুধু এটুকুই জানে যে পদ্ম ফোটার সময় হলে, রোদ্দুরে কাঁচা হলুদের রং লাগলে বেরিয়ে পড়তে হয়। বেরিয়ে পড়তে হয় চেনা গণ্ডির বাইরে, নীল আকাশে মেঘের ভেলায় ভেসে। না হলে প্রতিদিনের থোড়-বড়ি-খাড়া আর খাড়া-বড়ি-থোড় আমাদের অন্তরাত্মা হাঁফিয়ে ওঠে। ভ্রমণের উদ্দেশ্য তো শুধু দেশ পরিচয় নয়, মানুষজনকে জানাও নয়। ভ্রমণ প্রকৃতির পাঠশালায় জীবনের সহজপাঠ।
ভ্রমণ শব্দের যে অর্থ আজ আমরা বুঝি অষ্টাদশ শতকে তাকে শুধুই তীর্থযাত্রা বোঝাত। একটু ব্যাপক অর্থে দেবদর্শন এবং বেড়ানো দুই-ই একসঙ্গে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ বসু (১৯১৫ সাল) বলেছেন– “শ’দেড়েক বছর আগে বাঙালির ভ্রমণের অর্থই ছিল তীর্থভ্রমণ। যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের পিতা) ‘ব্যয়রামের উপশমের জন্য’ জগন্নাথধাম যাত্রা করেন। অম্লশূলের রুগি যদুনাথ সর্বাধিকারী সংসারে বীতশ্রদ্ধ হয়ে সুদূর উত্তরভারতে গমন করেছিলেন। এই ভ্রমণ ছিল নিছকই তীর্থযাত্রা, গয়া, কাশী, বৃন্দাবন পরিক্রমার মতো। উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি থেকে রেলপথ চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তীর্থযাত্রার আকর্ষণটা ফিকে হয়ে আসতে শুরু করে। আসলে রেলের গাড়ি সমগ্র ভারতের মানচিত্রটাই বদলে দেয়, বদলে যায় ভারতবাসীর মানসিকতা। ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকে কিছু শিক্ষিত বাঙালির হাত ধরে তীর্থযাত্রা রূপান্তরিত হয় নিছক পর্যটনে। আর সেকালে পর্যটন বলতে পুজোর ছুটির দীর্ঘ অবকাশে হাওয়া বদল, স্বাস্থ্যোদ্ধার ইত্যাদি ইত্যাদি।…”
সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমণের উদ্দেশ্য, ব্যাপ্তি ও প্রকরণ বদলেছে। ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি থেকে তীর্থভ্রমণ থেকে বিশুদ্ধ দেশভ্রমণ অন্য খাতে বইতে শুরু করে। ডাক্তার কবিরাজের পরামর্শে পেটরোগা বাঙালির হাওয়া বদলের শুরু। চেঞ্জারবাবুরা দুগ্গা দুগ্গা বলে বাক্সপ্যাঁটরা (মায় সঙ্গে হাঁড়ি কড়া জলের কলসি শিলনোড়া ইত্যাদি) সহ পুরো সংসারটা রেলগানির কামরায় পুরে হাজির হত পশ্চিমের কোনও জনশূন্য স্টেশনে। সেদিনের মধুপুর, গিরিডি, শিমূলতলা কিংবা দেওঘর স্বাস্থ্য উদ্ধারকারী বাঙালির বৈকালির পদচারণা আর দেহাতি হাটে ভোজনবিলাসী ড্যাঞ্চিবাবুদের সমাগমে পূর্ণ হয়ে উঠত।
ড্যাঞ্চিবাবুকাদের বলে মনে আছে? বাঙালি যারা শুধু খেতে, ঘুমোতে আর খাওয়ার গল্প করতে পশ্চিমে পাড়ি দিতেন, স্থানীয় হিন্দিভাষীরা তাদের ড্যাঞ্চিবাবু বলত। দেহাতি হাটে তারা গাদা গাদা শাকসবজি, গণ্ডা গণ্ডা দেশি মুরগি, ডজন ডজন মুরগির ডিম, নধর ছাগলছানা কিনে মুটের মাথায় চাপিয়ে বাসায় ফিরতে ফিরতে সঙ্গী অপর কোনও বাঙালিবাবুকে গদগদ স্বরে বলতেন, মশাই, বুইলেন কিনা, এখানে সবই ড্যাম চিপ। এই ড্যাম চিপ থেকেই ড্যাঞ্চিবাবু। সেই ড্যাঞ্চিবাবুরা হারিয়ে গেছে, হারিয়ে গেছে পশ্চিমের হাওয়া-বদলের অলস দিন। এক বছর মধুপুর থেকে গিরিডি যাচ্ছিলাম ট্রেনে। রেলগানির কামরায় এক অন্ধ ভিক্ষা করতে করতে গাইছিল—‘আধাচিড়ে আর গুড়, সবসে আচ্ছা মধুপুর।’ মধুপুরের আজ মধু নেই, শুকিয়ে গেছে গিরিডির উস্রী নদীর ঝরনা। ভেঙে পড়া গুটিকয় বাড়ি আর আগাছায় ভরা বাগান সেদিনের সোনালি স্মৃতি নিয়ে মুখ লুকিয়েছে মফস্বলের আনাচে কানাচে।
এখন ভ্রমণ আর বাঙালি অবিচ্ছেদ্য হয়ে গেছে। পুজোর ছুটি মানে শেষ রাতে উঠে ঘুম ঘুম চোখে অনেকটা পথ হেঁটে টাইগার হিলে সূর্যোদয়ের অপেক্ষা কিংবা রাজস্থানের বালিয়াড়িতে বসে লাল সূর্যটাকে টুপ করে ডুব দিতে দেখা। শারদীয়া মানে ঘর পালিয়ে তরাই-এর জঙ্গলে গাছেদের ঘ্রাণ নিতে নিতে দূরে একফালি কাঞ্চনজঙ্ঘার দিকে তাকিয়ে থাকা, কিংবা নৌকায় চড়ে বারাণসীর ঘাটে ঘাটে মন্দির, মানুষজন ও সনাতন ভারতবর্ষকে দেখে বেড়ানো। এ সবই আজ সব বাঙালির সাধ ও সাধ্যের মধ্যে। শুধু নদীর চরে চরে কাশফুল দুলে ওঠার প্রতীক্ষা, আর তখনি বেরিয়ে পড়া যে দিকে মন চায়। বাঙালির মন তো সদা চঞ্চল, সদাই সুদূরের পিয়াসী।
রচনাটি পুনঃপ্রকাশিত হল